৩৬ বছর বয়স মাত্র! এইটুকু পার্থিব জীবনে যা লিখেছেন তার ধাক্কা সামলাতে ১০০ বছর পরও বাঙালী হিমসিম খায়। বলছিলাম সুকুমার রায়ের কথা। ননসেন্স রাইমসের উদ্ভাবক এই মানুষটি যে শুধু ননসেন্স রাইমস বা হাস্যরসাত্মক লেখা লিখেই থেমেছিলেন তা-ও নয়। সায়েন্স ফিকশন, সিরিয়াস কিংবা অনুভূতি নিয়ে খেলা করার মতোও অনেক লেখা ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। আসুন এই অসম্ভব প্রতিভাধর রসাত্মক মানুষটির জীবনের কিছু ঘটনা জেনে আসি।
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের দুটি ছিল চরিত্র হাসি ও তাতা। সেই থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে উপেন্দ্রকিশোর রায়চৌধুরি ছেলে এবং মেয়ের নাম ডাকনাম রাখলেন। তাই সুকুমারের ডাকনাম ছিল ‘তাতা’।
তাতা ছোটকাল থেকেই ছিল প্রচণ্ড চঞ্চল, ফুর্তিবাজ। সব কিছুতে উৎসাহ, খেলাধুলোয় ওস্তাদ। যন্ত্রের সব খেলনা ঠুকে ঠুকে দেখত সে, কী করে চলে। বাদ্যযন্ত্র ভেঙে দেখত, কোথা থেকে আওয়াজ আসে। প্রচণ্ড কৌতুহল সবকিছুতে। আবার দুষ্টুমীতেও সেরা! ছোট লাঠি হাতে ছাদময় তাড়া করে বেড়াত বাড়ির বোর্ডিংয়ের মেয়েদের।
ছোট্ট বয়সেই চমৎকার গল্প বলতে পারত তাতা। উপেন্দ্রকিশোরের বিশাল একটি বই থেকে জীবজন্তুর ছবি দেখিয়ে টুনি, মণি আর খুসীকে (তার বোনেরা) আশ্চর্য মজার গল্প বলত। বই শেষ হয়ে গেলে জীবজন্তুর গল্প বানাত—মোটা ভবন্দোলা কেমন দুলে থপথপিয়ে চলে, ‘মন্তু পাইন’ তার সরু গলাটা কেমন গিঁট পাকিয়ে রাখে, গোলমুখে ভ্যাবাচোখ কম্পু অন্ধকার বারান্দার কোণে দেওয়ালের পেরেকে বাদুড়ের মতো ঝুলে থাকে ইত্যাদি। ছোটকাল থেকেই গল্প আর হাস্যরসের কমতি ছিল না সুকুমারের মাঝে।
‘রাগ বানাই’ বলে একটা খেলা ছিল তাতার। তার নিজেরই তৈরি। হয়তো কারও উপরে রাগ হয়েছে, কিন্তু শোধ নেওয়ারও উপায় নেই। তখন সে ‘আয়, রাগ বানাই’ বলে সেই লোকটার সম্পর্কে অদ্ভুত অদ্ভুত সব গল্প বানিয়ে বলতে থাকত। তার মধ্যে বিদ্বেষ বা হিংস্রভাব থাকত না, কোন ক্ষতি করার কথাও থাকত না, কেবল মজার কথা। তার মধ্য দিয়েই রাগ একবারে শেষ! এ থেকেই বোঝা যায় ছোটকাল থেকেই মানুষের প্রতি কতটা সহনশীল ছিলেন।
তার এক মাস্টারমশাই ছিলেন বড় ভাল মানুষ, কিন্তু কড়া বায়োস্কোপ-বিরোধী। একবার ক্লাসে সে বিষয়ে নিজের যুক্তি দেয়ার পরে প্রিয় ছাত্র সুকুমারকেও কিছু বলতে অনুরোধ করেন মাস্টারমশাই। সুকুমার বলেন, কিছু ছবি খারাপ, সেগুলো না দেখাই ভালো, কিন্তু ভালো ছবিও আছে, আর সে সব দেখলে অনেক কিছু শেখা যায়। মাস্টারমশাই একটু রাগই হন। সুকুমার জানতে চান, আপনি বায়োস্কোপ দেখেছেন? ‘আমি ওসব দেখি না’— কড়া জবাব দেন মাস্টারমশাই। জোর করে মাস্টারমশাইকে নিয়ে একটা ভাল ছবি দেখাতে নিয়ে যান সুকুমার। ছবি শেষে মাস্টারমশাই জানান, ‘তুমি আমার একটা মস্ত ভুল ভাঙিয়ে দিলে।’
বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সুকুমারের নাটকের শখ বাড়ে। ছেলেবেলায় অন্যের লেখা কবিতা বা গল্পের নাট্যরূপ দিয়ে ভাইবোন, আত্মীয়, বন্ধুদের নিয়ে অভিনয় করা হত, এ বার নিজে নাটিকা লেখা ধরলেন। তবে অভিনয়ের লোক তো লাগবে! তাই বন্ধুবান্ধব নিয়ে তৈরি হয়ে গেল ‘ননসেন্স ক্লাব’। সাদাসিধে অনাড়ম্বর ভাবে আয়োজিত নাটকগুলো শুধু নাটকের গুণেই জনপ্রিয় হয়ে যেত। প্রায় প্রত্যেকটি নাটকেরই কেন্দ্রে থাকত কিঞ্চিৎ হাঁদা-প্রকৃতির একটি চরিত্র, যে আসলে নাটকের খুঁটি। ওই ভূমিকায় সুকুমার নিজেই অভিনয় করতেন।
‘তত্ত্বকৌমুদী পত্রিকা’র বিমলাংশুপ্রকাশ রায়ের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ‘তাঁর নাটকের দল গড়ে উঠেছিল অতি সহজ, স্বাভাবিকভাবে, যেমন জলাশয়ের মধ্যেকার একটা খুঁটিকে আশ্রয় করে ভাসমান পানার দল গিয়ে জমাট বাঁধে। সত্যই তিনি খুঁটিস্বরূপ, আমাদের অনেকের আশ্রয়।’ ননসেন্স ক্লাবের একটি হাতে লেখা পত্রিকাও প্রকাশ করতেন সুকুমার রায়, নাম ‘সাড়ে-বত্রিশ ভাজা’। বত্রিশ রকমের ভাজাভুজি আর তার উপরে অর্ধেক মরিচ বসানো, তাই সাড়ে বত্রিশ। সম্পাদক সুকুমার, মলাট ও অধিকাংশ অলঙ্করণ তাঁর, বেশির ভাগ লেখাও। সম্পাদকের পাতা ‘পঞ্চতিক্তপাঁচন’ বড়রাও আগ্রহ নিয়ে পড়তেন। ঠাট্টা থাকত, তবে খোঁচা নয় শুধু মজা আর নির্মল আনন্দ।
ব্রিটেনে পড়তে গিয়ে ছাপার প্রযুক্তি বিষয়ে অত্যন্ত বিশেষ জ্ঞান অর্জন করেন সুকুমার। ১৯১৩ সালের সেপ্টেম্বর মাসে ‘ফেলো অব দ্য রয়্যাল ফোটোগ্রাফিক সোসাইটি’ উপাধি নিয়ে দেশে ফেরেন। এমনই চেয়েছিলেন তাঁর বাবা উপেন্দ্রকিশোর। সুকুমার বাংলা সাহিত্য জগৎকে সমৃদ্ধ করেছেন, সে আমরা জানি। কিন্তু বাংলা মুদ্রণ জগৎকেও অনেকখানি এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল ব্রিটেন থেকে তার অর্জিত জ্ঞান।
কোলকাতায় ফেরার পর তাঁর ১০০ নং গড়পার রোডে জমে ওঠে এক আড্ডার আসর। কখনও রসের আলাপ, কখনও গম্ভীর কথাবার্তা। তবে বাধ্যতামূলক ছিল ভালো খাওয়াদাওয়া। সোমবারে আসর বসত তাই নাম ‘মান্ডে ক্লাব’। খাওয়ার বাহার দেখে কেউ একটু ব্যঙ্গ করে বলতেন ‘মণ্ডা ক্লাব’। কামাক্ষীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়ের লেখায় পাওয়া যায়—Monday Club নামে তিনি এক সাহিত্য-আসর প্রতিষ্ঠা করেন। বহু গণ্যমান্য লোক এই ক্লাবের সভ্য ছিলেন। যেমন: সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত, নির্মলকুমার সিদ্ধান্ত, অতুলপ্রসাদ সেন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, কালিদাস নাগ, অজিতকুমার চক্রবর্তী, সুবিনয় রায়, জীবনময় রায়, চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, কিরণশঙ্কর রায়, ইত্যাদি।
১৯২১ সালের মে মাসে অসুস্থ হয়ে পড়েন কালাজ্বরে। ছেকে সত্যজিতের কেবল তখন জন্ম হয়েছে। চিকিৎসার জন্য নিয়ে যাওয়া হয় দার্জিলিংয়ের লুইস জুবিলি স্যানাটোরিয়ামে। কিন্তু এই দুরারোগ্য অসুখের ওষুধ তখনও আবিষ্কৃত হয়নি। আস্তে আস্তে স্বাস্থ্যের অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯২৩ সালের ২৯ আগস্ট তখন খুবই অসুস্থ সুকুমার। গান শুনতে ভালবাসতেন। ২৯ আগস্ট রবীন্দ্রনাথ এসে তাঁকে নয়টি গান শোনান। তবে শরীর দ্রুত খারাপ হচ্ছিল। কয়েক দিন পর ১০ সেপ্টেম্বর মৃত্যু হয় এই ক্ষণজন্মা নক্ষত্রের।
তথ্যসূত্র: আনন্দবাজার পত্রিকা, প্রস্তুতি পর্ব বিশেষ সংখ্যা: সুকুমার রায়, নানা সুকুমার: কোরক সংকলন, সুকুমার: লীলা মজুমদার, সুকুমার রায় জীবনকথা: হেমন্তকুমার আঢ্য










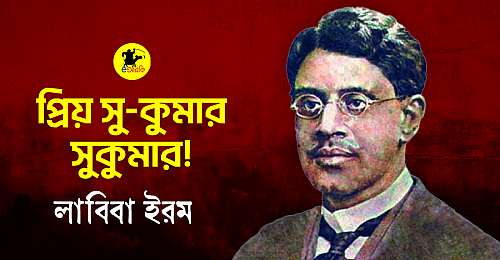
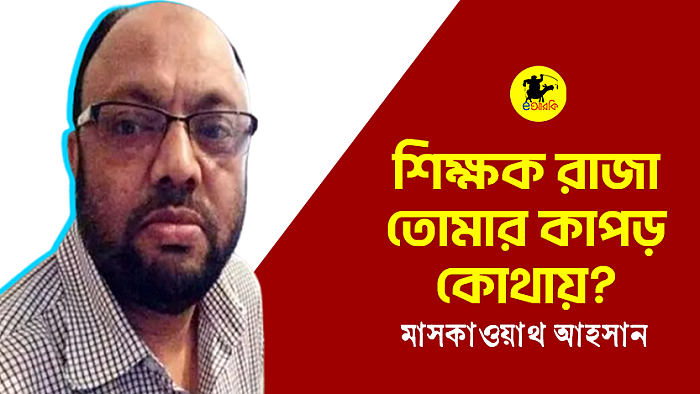

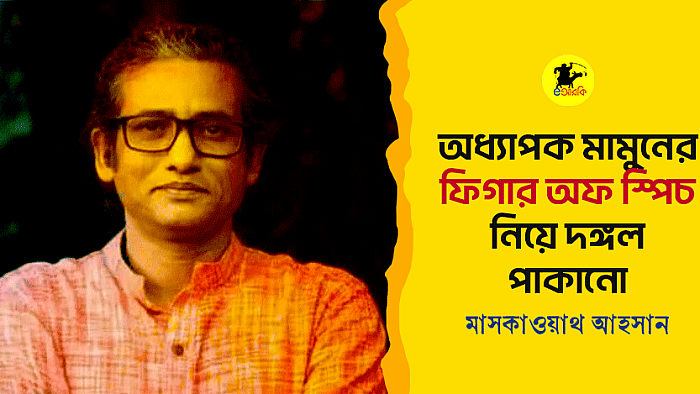

















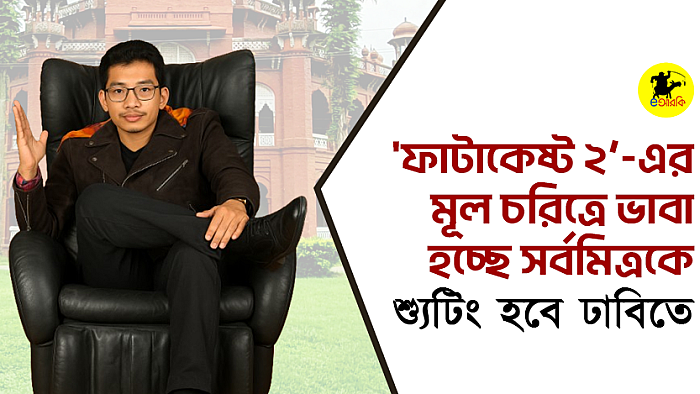

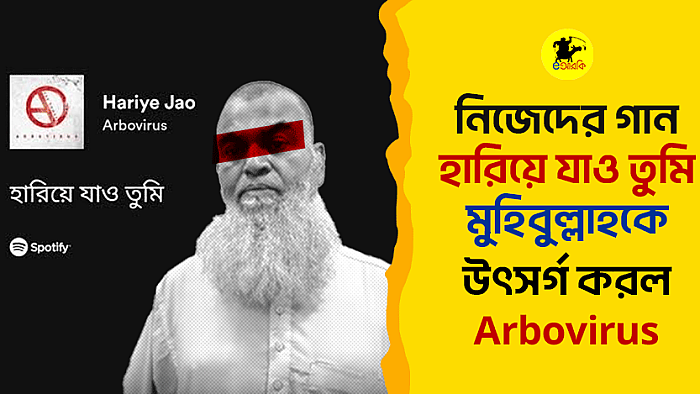

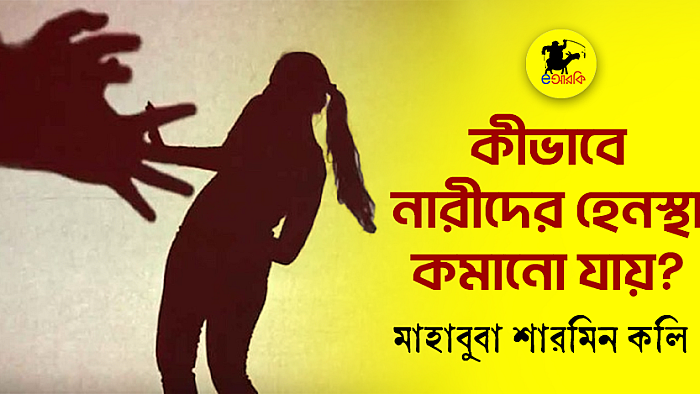
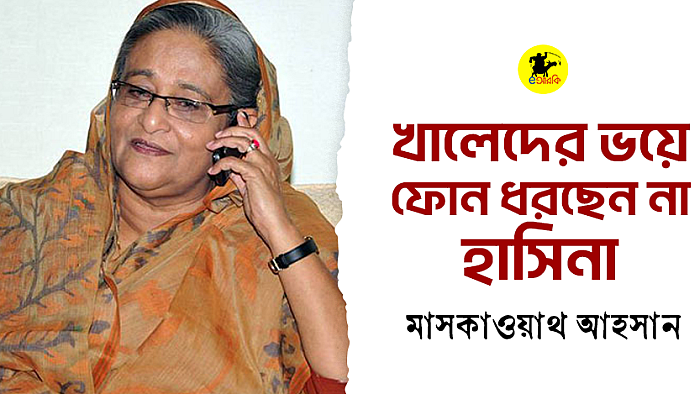






পাঠকের মন্তব্য