১৯৩৯ সালের ১ সেপ্টেম্বর পোল্যান্ডে জার্মান বাহিনীর আগ্রাসনের মাধ্যমে শুরু হয়ে যায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ। শুরুর প্রথম কিছুদিন এই যুদ্ধ বিশ্বযুদ্ধের ‘মর্যাদা’ পায়নি। কিন্তু একটা সময় জার্মানির সাথে ইতালি আর জাপানের যোগ দেওয়া এবং অন্যদিকে মিত্রপক্ষে ইংল্যান্ডের সাথে আমেরিকা ও রাশিয়ার যোগ দেওয়ার পর অন্য মাত্রা পায় বিশ্বযুদ্ধ। সেই সময় ভারতীয় উপমহাদেশ তথা পুরো বাংলা ছিল ব্রিটিশ শাসনাধীন। প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে ত্রাস সৃষ্টি করে একটা পর্যায়ে জাপানি বাহিনী নজর দেয় বাংলা ও আসামের সীমান্তবর্তী বার্মার দিকে। তখন থেকেই ভারতবর্ষের পূর্ব সীমানাও সরাসরি যুদ্ধের শিকার হয়। পরাধীন এক জাতি হয়েও যুদ্ধের ভয়াবহতা গ্রাস করেছিল পূর্ব বাংলার সাধারণ অধিবাসীদের।
জয়নুল আবেদীনের কল্যাণে যে দুর্ভিক্ষের ছবি আমাদের কাছে খুব পরিচিত সেই তেতাল্লিশের মন্বন্তর ঘটেছিল এই বিশ্বযুদ্ধের সময়ই, যুদ্ধের প্রত্যক্ষ প্রভাবে। বোমার বিস্ফোরণ নেই, গুলির শব্দ নেই, যুদ্ধের কোন দৃশ্যমান নমুনা নেই; অথচ এই যুদ্ধের প্রভাবে সৃষ্ট দুর্ভিক্ষ কেড়ে নিয়েছিল প্রায় ৩০ লাখ বাঙালির প্রাণ। বিশ্বযুদ্ধের স্বভাবজাত ধ্বংসযজ্ঞ দেখতে হয়নি বলে বিশ্বজুড়ে প্রায় সাড়ে সাত কোটি প্রাণ কেড়ে নেওয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ নিয়ে বাংলাদেশে তেমন একটা কথা হতে দেখা যায় না। তবে বাঙালি কথাসাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের জীবনী ‘অর্ধেক জীবন’ বইয়ে পূর্ব বাংলায় দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ভয়াবহতার কিছু কথা পাওয়া যায়।
অবিভক্ত বাংলার ফরিদপুরে জন্ম নেওয়া এই সাহিত্যিকের শৈশব কেটেছিল এই বাংলাতেই। বিশ্বযুদ্ধের শুরুর সময়টায় যদিও ছিলেন কলকাতায়, তবে কলকাতা জাপানি আক্রমণের শিকার হবার পর ফিরে আসতে হয়েছিল গ্রামে। সেখানেই কেটেছিল তার যুদ্ধের বাকি সময়টা। সরল শৈশবের মাঝেও দেখেছিলেন যুদ্ধের ভয়াবহতা। মহাযুদ্ধের সেই স্মৃতিকথা ‘অর্ধেক জীবন’ বই থেকে খানিকটা সংক্ষেপিত আকারে থাকল eআরকি পাঠকদের জন্য।

রবীন্দ্রনাথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের শুরুটা দেখে গেছেন, তখনও তা ইউরোপে সীমাবদ্ধ। অচিরকালের মধ্যেই তা দাবানলের মতন ছড়িয়ে পড়ে। ভারতীয়দের কাছে এ এক কিম্ভূত যুদ্ধ। পরাধীন দেশ, সে আবার কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করবে, তার কোনও পক্ষ বা বিপক্ষ থাকার কথা নয়। কিছু শাসকশ্রেণী ভারতকেও যুদ্ধে জড়িয়ে নিল, কারণ এত বড় উপনিবেশটির সম্পদ যুদ্ধের কাজে লাগাতে হবে। ভারতীয় সৈনিকদের রণক্ষেত্রে পাঠাতে হবে কামানের খাদ্য হিসেবে।
আমেরিকার যুদ্ধে যোগদান ও জাপান সিঙ্গাপুর দখল করার পর কলকাতাতেও সাজ সাজ রব পড়ে যায়। পূর্ব রণাঙ্গনে জাপানিদের হাতে খুব মার খাচ্ছে ইংরেজরা, হাতছাড়া হয়ে যাচ্ছে কলোনিগুলো। রেঙ্গুন পতনের পর মনে হল জাপানিরা এসে গেছে একেবারে ভারতের দোরগোড়ায়, এরপর ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের দ্বিতীয় বৃহত্তম শহর কলকাতা দখলের জন্য ঝাঁপিয়ে পড়বে। ইংরেজদের সাহায্য করবার জন্য এসে গেছে আমেরিকান বাহিনী, শহরের পথে পথে অনবরত সামরিক গাড়ি ছুটছে। রেড রোডকে রানওয়ে বানিয়ে সেখান থেকে উড়ছে বিমান। সন্ধের পর সাড়া শহর প্রায় নিস্প্রদীপ, রাস্তার গ্যাসের আলোয় পরানো হয়েছে ঠুলি, সাধারণ নাগরিকরা বাড়ির মধ্যে বাতি জ্বাললেও জানলা খুলতে পারবে না, যখন তখন বিকট শব্দে বেজে উঠছে বিপদসঙ্কেত জানাবার জন্য সাইরেনের মহড়া। ফাঁকা মাঠ আর পার্কগুলিতে কাটা হয়েছে ট্রেঞ্চ, রাস্তার যেখানে সেখানে গাঁথা হয়েছে নতুন পাঁচিল। গোলাগুলি থেকে বাঁচবার জন্য যেগুলিকে বলে ব্যাফল ওয়াল, বাঙালিরা ঠাট্টা করে বলত, বিফল প্রাচীর।
যুদ্ধে অনেক কিছুই বদলায়। সব চেয়ে বেশি বদলায় মূল্যবোধ। প্রশাসনের দৃষ্টি অন্য দিকে থাকে বলে সেই সুযোগ নিয়ে কিছু কিছু মানুষের অবদমিত লোভ, হিংসা, কাম প্রবৃত্ত প্যান্ডোরার বাক্সের ভয়ঙ্কর পতঙ্গগুলির মতন বেরিয়ে আসে। খাদ্য, বস্ত্রের মজুতে যখন টান পড়ে, তখন শুরু হয় কালোবাজার। নারীদেহেরও বাজার তৈরি হয়। সৈনিকদের মনোরঞ্জনের জন্য রমণী সরবরাহ সব যুদ্ধেরই অঙ্গ। তাদের প্রকাশ্য বেলেল্লাপনা দেখলেও সরকার মুখ ফিরিয়ে থাকে। কলকাতা শহরে বারাঙ্গনার সংখ্যা কম নয়, তাতেও প্রয়োজন মেটেনি। অর্থের লোভে অনেক মধ্যবিত্ত পরিবারের সুন্দরী কন্যারা প্রকাশ্যে টমিদের কণ্ঠলগ্না হয়েছে। সমাজ তখন অদৃশ্য। তবে সব সৈনিকই যে শুধু নারী-সম্ভোগের জন্য উন্মত্ত, তা বলা যায় না। বহু দূরে ফেলে আসা স্ত্রী-পুত্র-কন্যাদের জন্যও অনেকের মন কেমন করত, প্রকাশ পেত বাৎসল্যের। ট্রেনের জানলায় বসা কোনও সৈনিকের ব্যথাময় মুখও দেখা যেত, অনুগ্রহ ভিখারি বাচ্চা ছেলেমেয়েদের প্রতি এক দৃষ্টিতে চেয়ে আছে। খুলনা স্টেশনে একজন সৈন্য ট্রেন থেকে আমার দিকে একটা চকোলেটবার ছুঁড়ে দিয়েছিল।
রবীন্দ্রনাথের মৃত্যুর পরের বছর শীতকালে একদিন জাপানিরা কলকাতায় হঠাৎ বোমা ফেলে গেল। ঠিক আক্রমণ বলা যায় না। কেমন যেন অন্যমস্কভাব। যেন বিমানে চেপে আকাশে বেড়াতে বেড়াতে কলকাতা পর্যন্ত চলে এসে জাপানিরা ভাবল, দু’একটা বোমা ফেলে একটু ভয় দেখানো যাক না! তাতেই শুধু ভয় নয়, দারুণ আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়ল শহরে। এতদিন যুদ্ধ চলছিল দূরে দূরে, এবার বুঝি কলকাতা শহর ধ্বংস হয়ে গেল। প্রায় দুশো বছর আগে সেই যে সিরাজউদ্দোল্লা কলকাতার দিকে কামান দেগেছিল, তারপর থেকে তো আর কলকাতার ওপর কোনও আক্রমণ হয়নি! দিশেহারার মতন নাগরিকরা পালাতে লাগল শহর ছেড়ে, যে সব পরিবারের সঙ্গতি আছে, তারা আশ্রয় নিল মধুপুর, দেওঘর, ঘাটশিলার মতন স্বাস্থ্যকর জায়গায়, অন্যরা পালাল গ্রামে-গঞ্জে। শহর প্রায় ফাঁকা।
দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের অন্যতম শিকার আমার বাবা। স্কুল-কলেজ বন্ধ হয়ে গেল অনির্দিষ্টকালের জন্য, বেসরকারি স্কুলে ছাত্রদের মাইনে থেকেই শিক্ষকদের বেতন হয়। স্কুল বন্ধ, বাবা বেকার হয়ে গেলেন, তখন আর সংসার চালাবেন কী করে, আমাদের পাঠিয়ে দিলেন গ্রামের বাড়িতে।
সেবারে আমি মাইজপাড়া গ্রামের বীরমোহন বিদ্যালয়ে ভর্তি হই। টিনের চালের ঘর, বেশ পরিচ্ছন্ন, পেছন দিকে টলটলে জলের সুন্দর একটা বড় দিঘি। স্কুলটি আমাদের বাড়ি থেকে অনেকটা দূরে, হেঁটে যাওয়া ছাড়া উপায় নেই। হাঁটতে ভালোই লাগে, শুধু একটা বিশাল অশ্বথ গাছতলায় শ্মশান, সেখান দিয়ে চোখ বুজে যাই, হঠাৎ হঠাৎ সে গাছের কোটর থেকে ডেকে ওঠে তক্ষক সাপ সে সাপকে কখনও চোখে দেখা যায় না। তবু ডাক শুনলেই ছমছম করে বুক। আর একটা বাড়ি, সেটাও গাঙ্গুলিবাড়ি। কিন্তু তাঁরা খুব ধনী, অনেকখানি জায়গা নিয়ে তাঁদের প্রাসাদোপম হর্ম্য, শুনেছি তাঁদের বন্দুক আছে, এবং আছে একটা বিলিতি কুকুর, আমরা বলতাম ডালকুত্তা, তার গম্ভীর ঘেউ ঘেউ শুনলে রক্ত হিম হয়ে যায়। সে বাড়ির গেটের সামনেটা পার হতাম দৌড়ে।
টাউন স্কুলে আমাদের কোনও মুসলমান সহপাঠী ছিল না। গ্রামের স্কুলে হিন্দু-মুসলমান মিশ্র ছাত্র। হেডমাস্টার লস্কর সাহেবকে মনে হত চলন্ত পর্বত, কিন্তু তাঁর ব্যবহার ছিল নরম, তাঁর এক ছেলে হেডমাস্টার-পুত্র হওয়ার যোগ্যতায় বেশ অহংকারী ধরনের। প্রথম প্রথম আমি ছিলাম অন্যদের কাছে কৌতূহলের সামগ্রী। আমার গায়ে শহুরে গন্ধ, আমার মতন চেন লাগানো গেঞ্জি অন্যরা আগে দেখেনি। আমার একটি মাউথ অর্গান ছিল। সেটাও অনেকের কাছে অভিনব। ওই মাউথ অর্গানটি কিছুদিন পরে একটা উঁচু ক্লাসের ছেলে কেড়ে নেয়।
উঁচু ক্লাসের ছেলেদের জন্মগত অধিকার আছে মাঝে মাঝে ছোটদের চড়-চাপড় মারার। এ নিয়ে নালিশ জানানো আরও বিপজ্জনক। অর্থাৎ র্যাগিং সব জায়গাতেই চলে। উঁচু ক্লাসের একটি ষণ্ডামার্কা ছেলে নাদুস-নুদুস চেহারার ছোট ছেলেদের গলা জড়িয়ে ধরে জিজ্ঞেস করত, এই তুই আমার রানি হবি? রানি হওয়া কাকে বলে তখন বুঝতাম না। আমাকে অবশ্য কারুর রানি হতে হয়নি কখনও।
স্কুলে যেতাম গরম গরম ফেনাভাত খেয়ে। ঢেঁকি ছাঁটা লাল চালের ফেনাভাত, অপূর্ব তাঁর স্বাদ, ঘি জোটার প্রশ্ন নেই। ঘি খায় আমগ্রামের মামাবাড়ির ছেলেমেয়েরা, তাতে কী। আলুসেদ্ধ আর পুঁটি মাছ ভাজা, চমৎকার! তবে, যতই সুখাদ্য হোক, দিনের পর দিন তা কি মুখরোচক হতে পারে? কয়েক মাস পরে শুধু সকালে নয়, প্রতিদিন অন্য বেলাতেও ফেনাভাত।
গ্রামে যুদ্ধের কোনও রেশ নেই, কামান-বন্দুকের শব্দ দূরে থাক, এখানকার আকাশ দিয়ে কোনও বিমানও উড়ে যায় না। তবু যুদ্ধের ধাক্কা লাগে এই নিস্তরঙ্গ গ্রামগুলিতে। প্রথম আঘাত হানে রান্নাঘরে।
আমরা আর যুদ্ধের খবর কী জানি! শহরের তুলনায় গ্রাম্য জীবন অনেক স্বাধীন। কলকাতায় বাড়ি থেকে একা একা বেশি দূরে যাওয়া নিষেধ ছিল। পথ হারাবার ভয়, গাড়ি চাপা পড়ার ভয়। গাড়ি মানে, ট্রাম-বাস-মোটর গাড়ি, ঘোড়ার গাড়ি, গোরুর গাড়ি। প্রথম তিন প্রকার গাড়ি চাপা পড়লে নির্ঘাত মৃত্যু, ঘোড়ার গাড়ি চাপা পড়লে প্রাণটা না গেলেও দারুণ জখম হবার সম্ভাবনা, আর গোরুর গাড়িতে কেউ চাপা পড়লে তাকে কলকা থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হয়, সে শহরে বাস করার যোগ্য নয়। গ্রামে কোনও বাধাবন্ধন নেই, যেখানে খুশি টো টো করে ঘুরে বেড়ানো যায়। বর্ষা এসে গেছে, এখন চতুর্দিকে জল, ধানের খেতগুলিও বিল হয়ে গেছে, রাস্তা এখন নদী। আমি কবে যে সাঁতার শিখেছি, তাই-ই মনে নেই। মানুষ ছাড়া আর কোনও প্রাণীই জলে ডোবে না, গোরু-মোষ, এমনকী হাতিও জন্ম থেকে সাঁতরাতে পারে, মানুষের মাথা তাঁর শরীরের অনুপাতে বেশি ভারী, সহজে ডুবে যেতে চায়, তাই মাথাটাকে জলের ওপর তুলে রাখার জন্য সাঁতার শিখতে হয়। গ্রামে সাঁতার শেখার পদ্ধতিটি অতি সরল। মাসি, পিসি কিংবা দিদি স্থানীয়রা বাচ্চা ছেলেমেয়েদের হাসতে হাসতে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয়। শিশুটি ভয়ে চেঁচাতে চেঁচাতে হাত-পা দাপায়, তারপর একটু একটু করে ডুবতে থাকে, একেবারে ডুবলে ওই নারীগণের কেউ জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তাকে কোলে তুলে আনে। শিশুটির কান্না তামতে না-থামতেই আবার জলের মধ্যে ঝপাস। এই রকম প্রতিদিন চার-পাঁচবার, এবং চার-পাঁচদিন পরেই বাচ্চাটা কান্নার বদলে খলখল করে হাসে, হাঁসের মতন ভাসতে শিখে যায়। তারপর যার যার নিজের কৃতিত্ব।
সাঁতার শেখার পরেই নৌকো চালানোর যোগ্যতা অর্জন করতে হয়। যে সাঁতার জানে না, তাঁর বৈঠা কিংবা লগি হাতে নেওয়ার অনুমতি মেলে না। নৌকো বলতে যা বোঝায় তা আমাদের নিজস্ব ছিল না, কিন্তু কয়েকটা কলাগাছ একসঙ্গে বেঁধে নিলে হয় ভেলা, তা নিয়ে দিব্যি চলাচল করা যায়। জলপথে, এমনকী শুধুমাত্র একটা তালগাছের খোল দিয়েও বানানো হয় ডোঙা। ওই ভেলা বা ডোঙা উল্টে যেতে পারে যখন তখন, ওই দুটিতেই আমার প্রথম বৈঠা চালানোর শিক্ষা। কখনও সখনও অন্যের নৌকোয় জায়গা পেয়ে মাদারিপুর পর্যন্ত ঘুরে আসা ছিল দারুণ রোমাঞ্চকর অভিজ্ঞতা। এ যেন গণ্ডি পেরিয়ে যাওয়া, বৃত্তটা আরও বিস্তারিত হওয়া।
মাদারিপুর একটি গঞ্জ, অনেক দোকানপাট, অনেক খদ্দের ও ব্যাপারি। পাশের নদীটার নাম আড়িয়াল খাঁ। কলকাতায় পাশে গঙ্গা কতবার দেখেছি, আরও কত নদী পার হয়ে আসতে হয় এখানে, তবু আড়িয়াল খাঁ-ই আমার কাছে সবচেয়ে বেশি আকর্ষণীয়। নামটার মধ্যেই বিশেষ দার্ঢ্য রুয়েছে। আগে মনে করতাম, এ নদী বুঝি কোনও ডাকাতের নামে, পরে শুনেছি কোনও ফকিরের। বর্ষার সময় আড়িয়াল খাঁ-র রূপ কোনও লুঠেরার মতনই দুর্দান্ত, ঢেউ যেন ফুঁসছে, অনবরত পাড় ভাঙছে। নদী যেন কামড়ে কামড়ে খেয়ে নিচ্ছে তটরেখা।
নদীতে জাল ফেলে ধরা হচ্ছে ইলিশ মাছ। যেসব মাছের গায়ের রং একেবারে সাদা, তারা সূর্যের আলো সহ্য করতে পারে না। জল থেকে তোলার পরই মারা যায়, তাই জ্যান্ত ইলিশ সচরাচর কেউ দেখতে পায় না। এক একটা নৌকো ঘাটে এসে ভিড়লেই ক্রেতারা এসে ভিড় জমায়। ওজন-টোজনের কোনও বালাই নেই, মাছের আকার অনুযায়ী দাম। ক্রেতার তুলনায় মাছ অনেক বেশি, তাই বেশ দরাদরি চলে। একবার আমার কাকা দু’আনা (বারো পয়সা) দিয়ে একটা প্রায় দু’ কিলো সাইজের ইলিশ কিনলেন। দলটির মধ্যে আমিই সর্বকনিষ্ঠ, একজন জেলের হঠাৎ কী খেয়াল হল, একটা ছোট ইলিশ (ছ’-সাতশো গ্রাম) আমার দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, এটা দা ঠাউরের জইন্যি মাগনা দিলাম।
মাছের অভাব নেই, কিন্তু টান পড়ল অন্য দিকে। অনবরত ফেনাভাত রান্নার কারণ, চাল বাড়ন্ত। বাঙালিরা সাধারণত শখ করে দু’একদিন ফেনাভাত খায়, অন্য সময় ভাতের ফেন গেলে ফেলে দেওয়া হয়। কিন্তু চাল কম পড়লে ফেন দিয়েই পেট ভরাতে হবে। ক্রমে চাল একেবারেই অদৃশ্য হয়ে গেল।
জাপানিরা আসছে, জাপানিরা আসছে! জাপানের অগ্রগতি ইংরেজরা রুখতে পারেনি। রেঙ্গুন দখল করার পর জাপানি সৈন্যবাহিনী অসম পেরিয়ে নামবে পূর্ববঙ্গে, তাই সরকার থেকে সেখানকার চারটি জেলার সমস্ত ধান-চাল সরিয়ে নেওয়া হয়। যোগাযোগ ব্যবস্থা বিচ্ছিন্ন করার জন্য বাজেয়াপ্ত করা হল বহু নৌকো, কয়েক হাজার নৌকো একেবারে ধ্বংস করেই দেওয়া হল, সেখানকার মানুষগুলি কার্যত গৃহবন্দি, তারা খাবে কী? সে চিন্তা সরকারের নয়। এরকম কৃত্রিম অভাবের সময়ই শুরু হয় কালোবাজারের রমরমা। মজুতদারদের কল্যাণে চালের দর বাড়তে থাকে লাফিয়ে লাফিয়ে। যুদ্ধ পূর্বকালে চালের মন (৪০ সেরে এক মন, এখনকার ৩২-৩৩ কেজি) ছিল ছয় থেকে সাত টাকা। কোনও বছর আট টাকায় উঠলে লোকে বলত, দেশটার হল কী? তখন সোনার ভরি পঁয়তিরিশ টাকা চার আনা। বেয়াল্লিশ সালের ডিসেম্বরে চালের মন তেরো থেকে চোদ্দো টাকা, পরবর্তী এক বছরের মধ্যে তা পঞ্চাশ-ষাট, চট্টগ্রামে আশি টাকা, ঢাকায় একশো পাঁচ টাকা।
খাদ্যশস্যের প্রকৃত অভাবকে বলে দুর্ভিক্ষ। পরবর্তীকালে গবেষক অমর্ত্য সেন দেখিয়েছেন যে সেই তেতাল্লিশ সালে খাদ্যশস্য ছিল প্রয়োজনের পক্ষে যথেষ্ট, কিন্তু সরকার ও কালোবাজারিরা তাঁর অনেকখানিই সরিয়ে রেখেছিল, সেই জন্যই খোলা বাজারের চালের এমন আকাশছোঁওয়া মূল্যবৃদ্ধি, তা চলে গিয়েছিল সাধারণ মানুষের ক্রয়ক্ষমতার বাইরে। দেশে চাল আছে, তবু দেশের এক অংশের মানুষ অনাহারে ধুঁকছে।
আমার বাবা সেকালে মাইনে পেতেন পঁয়তাল্লিশ টাকা। স্কুল বন্ধ, তখন তাঁর সে উপার্জনও নেই। কলকাতায় তিনি অন্য চাকরি খুঁজছেন, কী করে টিকে আছেন, আমাদের জন্যই বা কী উপায়ে মাঝে মাঝে কিছু টাকা পাঠাচ্ছেন, সে জ্ঞান আমার ছিল না। এক দু’মাস কোনওই চিঠি আসত না তাঁর, কোথায় আছেন জানি না, হঠাৎ হঠাৎ দেখে ফেলতাম, ঘরের এক কোণে, দেয়ালের দিকে ফিরে, মুখে আঁচল চাপা দিয়ে নিঃশব্দে কাঁদছেন মা। শুধু মেয়েরাই বুঝি পারে এভাবে কাঁদতে, শরীরটা কাঁপে, কোনও শব্দ হয় না।
মাদারিপুরে চালের দোকানের সামনে অনেক মানুষ দাঁড়িয়ে আছে ম্লান মুখে। দোকানের মালিক হাত নেড়ে জানাচ্ছেন, চাল নেই, চাল নেই! সন্ধেয় অন্ধকারে সে দোকানেরই পেছনের দরজা দিয়ে সম্পন্ন গৃহস্থেরা থলে ভরা চাল নিয়ে সরে পড়ছে চুপি চুপি। এ দেশের মানুষ কেড়ে খেতে জানে না, নিজের কপালে হাত চাপড়ায়। সৈন্যদের জন্য প্রচুর খাদ্য গুদামবন্দি রয়েছে, সিংহলে রপ্তানি যাচ্ছে চাল, তবু এখানকার অভুক্ত মানুষরা লুঠতরাজ শুরু করেনি। ‘এই সব মূঢ়, ম্লান, মূক মুখে দিতে হবে ভাষা’, কে দেবে সেই ভাষা, সে নেতৃত্ব কোথায়?
আমাদের সম্পূর্ণ অনাহারে পড়তে হয়নি, কোনও এক বিস্ময়কর কারণে সে বছর আলু সস্তা ছিল। আলু খেয়েও মানুষ বেঁচে থাকতে পারে। জাপানিরা কি আলু খায় না? সরকার আলুও সরিয়ে দিল না কেন? আমাদের চাল কেনার ক্ষমতা নেই, বস্তায় ভরে আলু আনা হত। ভাতের হাঁড়িতে সেদ্ধ করা হয় সেই আলু। সকালে আলু, দুপুরে আলু, বিকেলে আলু, রাত্তিরে আলু। একসঙ্গে বেশি আলু খাওয়া যায় না, মুখে রোচে না। তাই একসঙ্গে অনেক আলু সেদ্ধ করা থাকে, আমরা ঘুরে ফিরে একটা-দুটো খাই। ইস্কুলেও আলু নিয়ে যাই পুঁটলি বেঁধে, আমার মতন আরও অনেকে, ইস্কুল থেকে নুন আর মরিচ দেবার ব্যবস্থা করা হয়, প্রত্যেক পিরিয়াডের পর দপ্তরি এসে হাইবেঞ্চে একটু একটু নুন আর কয়েকটা কাঁচা লঙ্কা দিয়ে যায়, মাস্টারমশাইরাও পাঞ্জাবির পকেট থেকে আলু বের করেন। মাস্টারমশাইদের অনুপস্থিতিতে খুদে ছাত্রদের মধ্যে হঠাৎ হঠাৎ শুরু হয়ে যায় আলু-যুদ্ধ, কামানের গোলার মতন আলু ছোঁড়াছুঁড়ি চলে, এক পক্ষ ইংরেজ, এক পক্ষ জাপানি।
দিনের পর দিন এই রকম, এক এক রাতে আমরা ধোঁওয়া ওঠা গরম ভাতের স্বপ্ন দেখি। মনে হয় যেন এ-জীবনে আর ভাত খাওয়া হবে না। সহপাঠীদের মধ্যে যে দু’চারজনের বাড়িতে ভাত রান্না হয়, তাঁদের মুখে আমরা ভাতের গল্প শুনি। হেডমাস্টারের ছেলেটি সেইরকম একজন সৌভাগ্যবান, সে অবজ্ঞার সঙ্গে একদিন বলল, তার একথালা ভাতের ওপর একটা আরশোলা (ওখানকার ভাষায় তেলাচোরা) এসে পড়েছিল বলে সে পুরো ভাতটা বাড়ির কুকুরকে খাইয়ে দিয়েছে। তৎক্ষণাৎ সেই কুকুরটির প্রতি আমাদের ঈর্ষা হয়। এ কাহিনী শোনাবার সময় সেই লস্কর-নন্দন জামার পকেট থেকে একটি মূল্যবান লাঠি লজেন্স বার করে দেখিয়ে দেখিয়ে চোষে।
বাজারে আলুও তো অফুরন্ত নয়, একদিন টান পড়বেই, তারপর? এরকম দুঃসময়ে চুরি-ডাকাতি ও অরাজকতাও বাড়ে। আমাদের বাড়িতেও চোর এল এক রাতে। আমাদের বাড়িটি ব্রাহ্মণপল্লীর অন্য বাড়িগুলির পেছন দিকে, তেমন মজবুতও নয়। মাটির ভিত, ইট-সিমেন্টের কোনও বালাই নেই, সেই মাটির ভিত শাবল দিয়ে খুঁড়ে সিঁধ কেটে ভেতরে তো ঢোকাই যায়। হায়রে চোরের পোড়া কপাল, আমাদের মতন বাড়িতে এসে সে কী পাবে? চোরেরা সাধারণত আগে থেকে খোঁজ খবর নিয়ে আসে, এ নিশ্চিত পেশাদার চোর নয়, পেটের জ্বালায় মরিয়া হয়ে ঢুকে পড়েছে।
শীতের রাত, মেঝেতে লম্বা বিছানা পাতা, কম্বল চাপা দিয়ে মায়ের দু’পাশে শুয়ে ঘুমোচ্ছি আমরা চার ভাইবোন। চোরটি ঘরের মধ্যে ঢুকে এসে হাতড়ে হাতড়ে কিছুই পায় না। আলনা থেকে পুরনো জামা-কাপড়গুলি নিয়ে পুঁটলি বাঁধল, কিন্তু শুধু তাতে তার পোষাবে কেন? শেষপর্যন্ত সে আমাদের গা থেকে কম্বল টেনে নিতে লাগল। শীত লাগতেই আমার ঘুম ভেঙে যায়, চেয়ে দেখি আবছা আলোয় প্রেতের মতন এক ছায়ামূর্তি। পরনে শুধু লেংটি, প্রায় উলঙ্গই মনে হয়, ওরা নাকি সাড়া গায়ে তেল মেখে আসে। কিছু না ভেবেই আমি চেঁচিয়ে ডাকলাম, মা! মা সঙ্গে সঙ্গে এক হাতে আমার মুখ চাপা দিলেন, অর্থাৎ মাও আগে জেগেছেন, কিন্তু সাড়াশব্দ করতে গেলেই যদি চোরটি শাবল দিয়ে মাথায় মারে, কিংবা পেটে ছুরি বসিয়ে দেয়। সন্তানদের মধ্যে সবচেয়ে বড় ছেলেটির বয়েস ন বছর, মীরা পঁচিশ বছরের তরুণী, তাঁর স্বামী থাকেন অনেক দূরে, রাত্তিরে ঘরের মধ্যে একজন জলজ্যান্ত পুরুষ, তার কাছে কী অস্ত্র আছে জানা নেই, এর চেয়ে অসহায় অবস্থা আর কী হতে পারে? সেই চোর কম্বল টেনে নিয়ে ধীরে সুস্থে গর্ত দিয়ে নেমে গেল। কাকে ডাকব, কে সাহায্য করবে, এত রাতে চোরের পিছু পিছু ধাওয়া করারও কোনও প্রশ্ন ওঠে না।
আমার একটি ছোট টিনের বাক্স ছিল, তাতে ছিল পাঠ্য বইয়ের বাইরের দু’একখানা বই, একটা দু’মুখো লাল-নীল পেন্সিল, কয়েকটা কাচের গুলি, কিছু সোডার বোতলের ছিপি, কয়েক পাতা জলছবি, সবই অকিঞ্চিৎকর, কিন্তু আমার কাছে বিশেষ মূল্যবান। পরদিন পাছ-পুকুরের ওধারের জঙ্গলে সুটকেসটি একেবারে তোবড়ানো ও খালি অবস্থায় খুঁজে পাওয়া যায়। কয়েকদিন পর বাজারের কাছে একটি ছেলেকে আমার চেন বসানো গেঞ্জিটি পরে ঘুরে বেড়াতে দেখি, ওরকম গেঞ্জি আর দ্বিতীয়টি থাকার কোনওই সম্ভাবনা ছিল না, কিন্তু ছেলেটির নাকি কিছু বলা যাবে না, প্রতিকারের কোনও উপায় নেই। পল্লীর বয়স্কদের কাছে নালিশ জানাতে তাঁরা চাপা বিষাদের সঙ্গে বলেছিলেন, চুপ করে থাক, ও নিয়ে ঘাঁটাঘাঁটি করিস না।



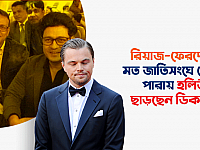



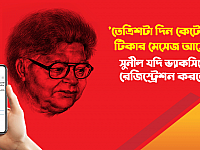






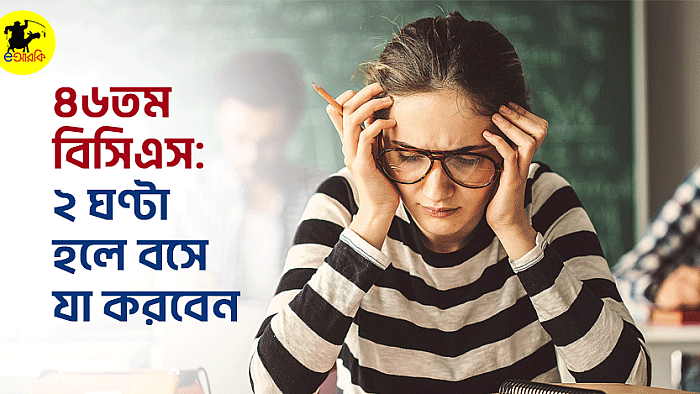




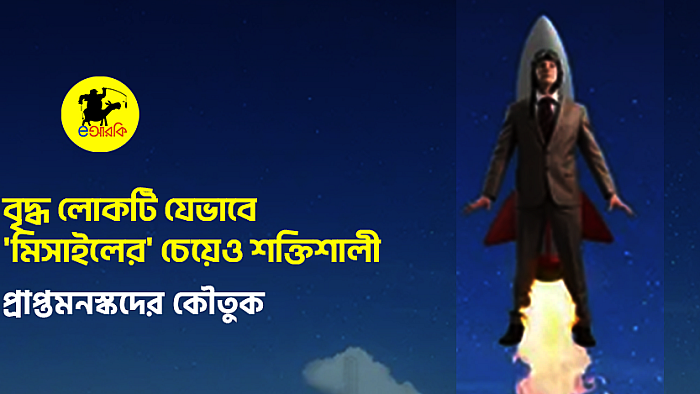



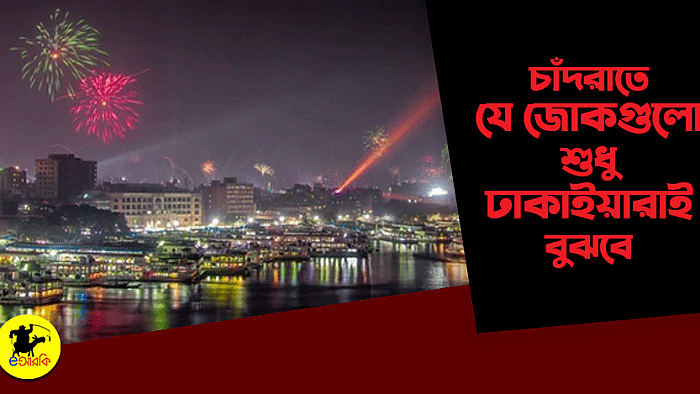


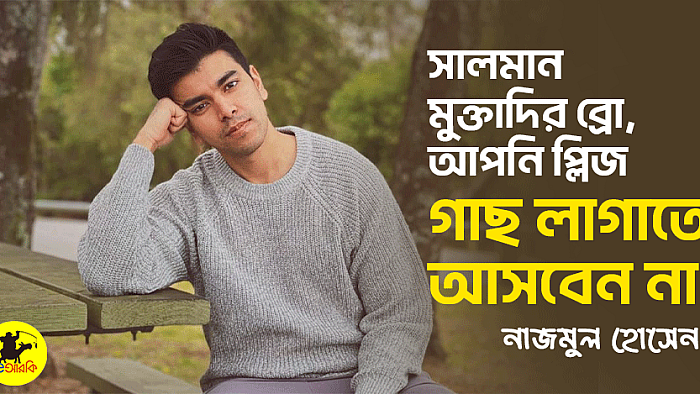

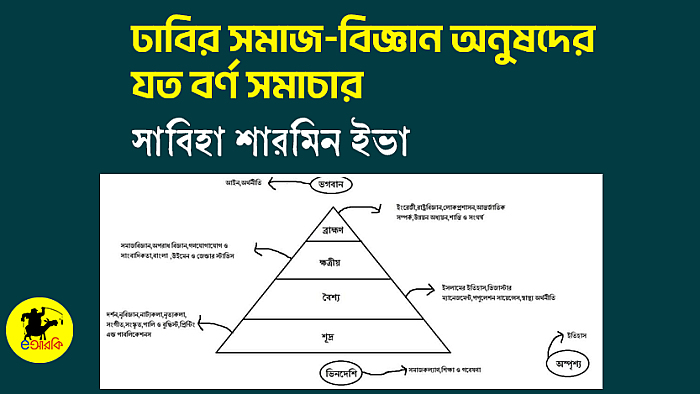




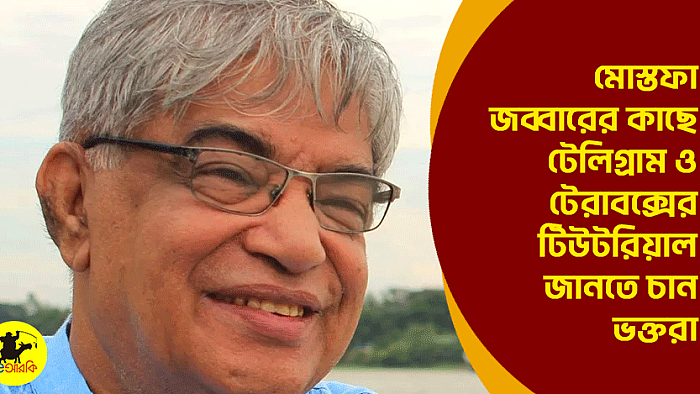






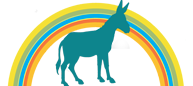

পাঠকের মন্তব্য
ইহাতে মন্তব্য প্রদান বন্ধ রয়েছে
লগইন